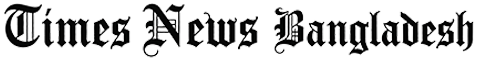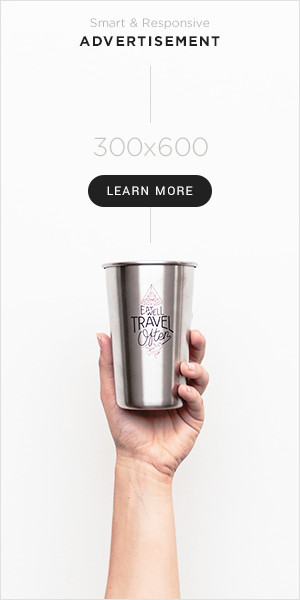ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে, আর এর ঢেউ এসে লেগেছে জার্মানির সামরিক নীতিতেও। একবিংশ শতকের শুরুতে, জার্মানি তার সামরিক শক্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার এক নতুন ও সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর সামরিক ব্যয় হ্রাস এবং শান্তির উপর জোর দেওয়ার দীর্ঘদিনের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে, জার্মান সরকার এখন সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সামরিক নীতি মূলত আত্মরক্ষামূলক এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সীমিত ছিল। “শান্তি লভ্যাংশ” (peace dividend)-এর ধারণার উপর ভিত্তি করে, দেশটির সামরিক বাজেট ক্রমশ হ্রাস পায় এবং Bundeswehr (জার্মান সেনাবাহিনী)-এর আকার ছোট হতে থাকে। অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণের উপরই মূলত জোর দেওয়া হয়েছিল।
তবে, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সবকিছু বদলে দিয়েছে। এই সংঘাত ইউরোপের নিরাপত্তার চিত্রকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এই পরিস্থিতিকে “Zeitenwende” বা “যুগান্তকারী পরিবর্তন” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, জার্মানি তার সামরিক শক্তিকে আধুনিকায়ন এবং ন্যাটোর প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ১০০ বিলিয়ন ইউরোর একটি বিশেষ তহবিল গঠন করবে। এর মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামরিক সক্ষমতা বাড়ানো।
জার্মান সরকারের নতুন সামরিক নীতিতে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে:
১. **Bundeswehr-এর আধুনিকীকরণ:** শুধুমাত্র সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো নয়, তাদের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামে সজ্জিত করাও এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সাইবার নিরাপত্তা এবং উন্নত লজিস্টিকস-এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
২. **সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি:** জার্মানির লক্ষ্য হলো ২০৩১ সালের মধ্যে Bundeswehr-এর কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। বর্তমানে প্রায় ১,৮০,০০০ কর্মী রয়েছে, এই সংখ্যাকে ২,০৩,০০০-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি অর্জনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যেমন –
* **ঐচ্ছিক সামরিক সেবা:** তরুণ-তরুণীদের জন্য সামরিক পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। উন্নত সুযোগ-সুবিধা, বেতন এবং কর্মজীবনের বিকাশের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।
* **রিজার্ভ বাহিনীর শক্তিশালীকরণ:** প্রয়োজনে দ্রুত মোতায়েন করা যায় এমন একটি শক্তিশালী রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত বাহিনীর উপর চাপ কমানো এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।
* **বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার বিতর্ক:** জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা ২০০৯ সালে স্থগিত করা হয়েছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়টি পুনরায় আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। যদিও সরকার এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি, তবে এটিকে একটি সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, লিথুয়ানিয়ায় জার্মান সেনাদের দীর্ঘমেয়াদী মোতায়েনের ফলে এই আলোচনা আরও গতি পেয়েছে।
৩. **প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:** সামরিক কর্মীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়।
সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর এই পথে জার্মান সরকারকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জার্মানির সামরিক ইতিহাসের সংবেদনশীলতা, বিশাল অঙ্কের অর্থায়ন, এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য কর্মী খুঁজে বের করা একটি বড় কাজ। জনমতের ক্ষেত্রেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই দেশের নিরাপত্তা জোরদারের পক্ষে থাকলেও, বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার মতো বিষয় নিয়ে এখনও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে সামরিক পেশার প্রতি আগ্রহী করে তোলাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
জার্মানির এই নতুন সামরিক নীতি শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যই নয়, সমগ্র ইউরোপ এবং ন্যাটোর জন্যও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে। জার্মানি ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং এর সামরিক শক্তিশালীকরণ ন্যাটোর পূর্ব প্রান্তে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জার্মানির ভূমিকাকে আরও দৃঢ় করবে এবং জোটের সম্মিলিত সক্ষমতা বাড়াবে।
জার্মান সরকার তার সামরিক নীতিতে যে পরিবর্তন এনেছে, তা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইউরোপের পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে এটি একটি অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার এই প্রচেষ্টা জার্মানিকে কেবল তার নিজের নিরাপত্তাই দেবে না, বরং ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে তার অবস্থানকে আরও মজবুত করবে। এই নতুন অধ্যায় জার্মানির ভবিষ্যৎ এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তার গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।